তৃতীয় পর্ব
রবির জীবনে মৃত্যুশোক
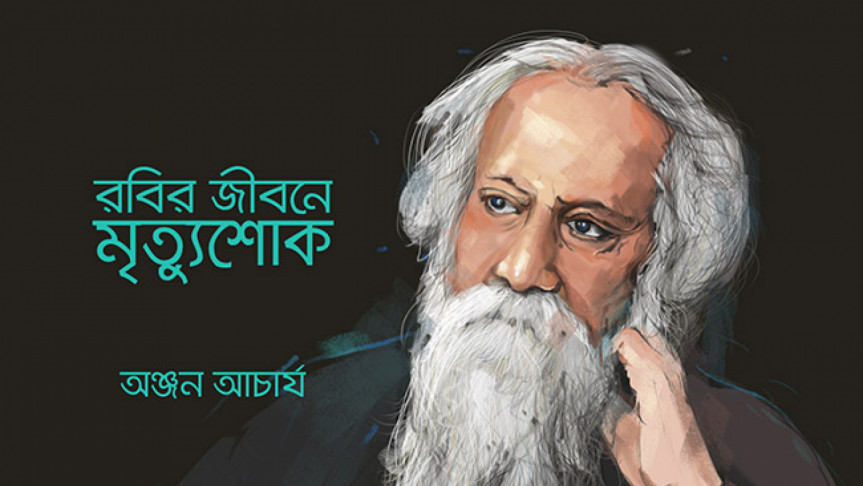
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক।
মৃত্যু : ২৬ চৈত্র ১৩০০ বঙ্গাব্দ, ৮ এপ্রিল ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ, বহুমূত্রজনিত রোগে ভুগে মারা যান।
‘বঙ্কিমচন্দ্র’ শিরোনামের প্রবন্ধটি ‘সাধনা’র বৈশাখ ১৩০১ সংখ্যার শেষ রচনা হিসেবে মুদ্রিত হয়। সেই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :
“একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতো এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্ম সংকীর্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক-একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্য সুর বাজিত তাহা আজ বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুবপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই তাঁহার স্বহস্তসম্পূর্ণ স্নেহপালিত ক্রোড়সঙ্গিনী বঙ্গভাষা আজ বঙ্কিমের জন্য অন্তরের সহিত রোদন করিয়া উঠিয়াছে। ...তিনিই আমাদের নিকট যথার্থ শোকের মধ্যে সান্ত্বনা, অবনতির মধ্যে আশা, শ্রান্তির মধ্যে উৎসাহ এবং দারিদ্র্যের শূন্যতার মধ্যে চির-সৌন্দর্যের অক্ষয় আকর উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন।...”
বিহারীলাল চক্রবর্তী
বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার। রবীন্দ্রনাথের বড় মেয়ে মাধুরীলতার শ্বশুর। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ‘ভোরের পাখী’ উপাধি দিয়েছিলেন।
মৃত্যু : ২৪ মে, ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ।
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তীর একনিষ্ঠ ভক্ত। ‘বিহারীলাল’ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :
‘বর্তমান নববর্ষের প্রারম্ভেই কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। বঙ্গের সারস্বতকুঞ্জে মৃত্যু ব্যাধের ন্যায় প্রবেশ করিয়াছে। তাহার নিষ্ঠুর শরসন্ধানে অল্পকালের মধ্যে অনেকগুলি কণ্ঠ নীরব হইয়া গেল। তন্মধ্যে বিহারীলালের কণ্ঠ সাধারণের নিকট তেমন সুপরিচিত ছিল না। তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা অল্প ছিল এবং তাঁহার সুমধুর সংগীত নির্জনে নিভৃতে ধ্বনিত হইতে থাকিত, খ্যাতির প্রার্থনায় পাঠক এবং সমালোচক-সমাজের দ্বারবর্তী হইত না। কিন্তু যাহারা দৈবক্রমে এই বিজনবাসী ভাবনিমগ্ন কবির সংগীতকাকলিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল তাহাদের নিকটে তাঁহার আদরের অভাব ছিল না। তাহারা তাঁহাকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া জানিত।’
কার্ল এরিখ হ্যামারগ্রেন
একজন ফরাসি-ভাষা শিক্ষক। সুইডেনবাসী এই মানুষটির কাছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফরাসি ভাষা শিখতেন।
মৃত্যু : ২০ আষাঢ় ১৩০০ বঙ্গাব্দ, ৩ জুলাই ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ, মঙ্গলবার।
রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘পথের সঞ্চয়’ বইয়ের ‘যাত্রার পূর্বপত্র’ প্রবন্ধে লিখেছেন :
‘য়ুরোপের যাঁহারা অসামান্য লোক তাঁহাদের কথা আমরা বইয়ে পড়িয়াছি, তাঁহাদিগকে কাছে দেখি নাই। কাছে যে দুই-একজনকে দেখিয়াছি য়ুরোপের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহারা স্থান পান নাই। অনেকদিন হইল একটি সুইডেনের মানুষকে দেখিয়াছিলাম, তাঁহার নাম হ্যামারগ্রেন। তিনি সেই দূরদেশে বসিয়া দৈবক্রমে রামমোহন রায়ের কি একটুকু পরিচয় কোনো একটা বইয়ে পাইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মনে এমন একটি ভক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহার দারিদ্র্য সত্ত্বেও দেশ ছাড়িয়া তিনি বহু কষ্টে সমুদ্র পার হইয়া এই বাংলাদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানকার ভাষা জানিতেন না, মানুষকে চিনিতেন না, তবু বাঙালির বাড়িতেই আশ্রয় লইয়া এই রামমোহন রায়ের দেশকেই তিনি বরণ করিয়া লইলেন। যে অল্প কয়দিন বাঁচিয়াছিলেন, কী দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়া, কী নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে, অথচ কী সম্পূর্ণ নম্রতার মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, তিনি এই দেশের হিতের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা কখনোই ভুলিতে পারিবেন না।’
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
রবীন্দ্রনাথের ভাইয়ের ছেলে, অগ্রজ বীরেন্দ্রনাথের একমাত্র সন্তান।
মৃত্যু : ৩ ভাদ্র ১৩০৬ বঙ্গাব্দ, ১৯ আগস্ট ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার ভোরে। ২৯ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই।
সুদর্শন, সুসাহিত্যিক এই ভাইয়ের ছেলেকে রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী দেবী নিজের ছেলের মতো স্নেহ করতেন। একটি তারিখহীন পত্রে [৩ ভাদ্র?] রবীন্দ্রনাথ বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লিখেছেন : ‘বলুর মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতায় থাকা আমার পক্ষে কষ্টকর হইয়াছে। বিশেষতঃ আমার স্ত্রী শিলাইদহে অত্যন্ত শোক অনুভব করিতেছেন, বলুর প্রতি তাঁহার একান্ত স্নেহ ছিল।’
মহারানী ভিক্টোরিয়া
ভারত-সম্রাজ্ঞী।
মৃত্যু : ৯ মাঘ ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, ২২ জানুয়ারি ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ, মঙ্গলবার।
রানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু প্রসঙ্গটি প্রশান্তকুমার পালের বইয়ে উল্লিখিত হয় এভাবে- ‘ভারত-সম্রাজ্ঞী’ ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু ঘটায় বেশ কিছুদিনের জন্য এদেশে সমস্ত আনন্দানুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। কালো বর্ডারে ঘেরা সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত অজস্র শোকসভার বিবরণ দেখে মনে হয়, সারা দেশে শোকপ্রকাশের যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল।
রবীন্দ্রনাথও ভারত-সম্রাজ্ঞী মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু উপলক্ষে শোক জ্ঞাপন করে একটি প্রবন্ধ লেখেন ও ১১ মাঘের সায়ংকালীন অধিবেশনে ‘প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া’ সেটি পাঠ করেন। রচনাটি ‘এক সপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ’-এর প্রতিবেদনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ‘তত্ত্ববোধিনী’র ফাল্গুন-সংখ্যায় এবং ‘সাম্রাজ্যেশ্বরী’ নামে ‘ভারতী’র ফাল্গুন-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। দুটি পাঠে অল্পবিস্তর প্রভেদ আছে, কিন্তু পার্থক্যটি গুরুতর নয়।
রবীন্দ্রনাথ ‘সাম্রাজ্যেশ্বরী’ নামের প্রবন্ধে শোক প্রকাশ করে বলেছেন : ‘ভারত সম্রাজ্ঞী মহারানী ভিক্টোরিয়া, যিনি সুদীর্ঘকাল তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্যের জননীপদে অধিষ্ঠাতা ছিলেন, যিনি তাঁহার রাজশক্তিকে মাতৃস্নেহের দ্বারা সুধাসিক্ত করিয়া তাঁহার অগণ্য প্রজাবৃন্দের নত মস্তকের উপর প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, ক্ষমা, শান্তি এবং কল্যাণ যাঁহার অকলঙ্ক রাজদণ্ডকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল, সেই ভারতেশ্বরী মহারাণী যে মহান পুরুষের নিয়োগে এই পার্থিব রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার প্রসাদে সুচিরকাল জীবিত থাকিয়া অনিন্দিতা রাজশ্রীকে দেশে কালে ও প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়ের মধ্যে সুদৃঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, অদ্য সমস্ত রাজসম্পদ পরিহারপূর্বক ললাটের মাণিক্যমণ্ডিত মুকুট আবরণ করিয়া একাকিনী সেই বিশ্বভুবনেশ্বরের নিস্তব্ধ মহাসভায় গমন করিয়াছেন। পরমপিতা তাঁহার মঙ্গল বিধান করুন।’
নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রবীন্দ্রনাথের বড় ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় সন্তান।
মৃত্যু : ২৭ ভাদ্র ১৩০৮ বঙ্গাব্দ, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার, রাত ২টায়, লিভারের রোগে আক্রান্ত হয়ে।
নীতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের খুব অনুগত ছিল। রবীন্দ্রনাথের পুত্র-কন্যাদের সাথে নীতীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের নানা চিত্র পাওয়া যায় পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘মাধুরীলতার চিঠি’তে এবং রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায়। তা ছাড়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রদত্ত যে জমির ওপর রবীন্দ্রনাথের ‘লালবাড়ি’টি নির্মিত হয়, তার স্থপতি ছিলেন নীতীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পুত্রের মতো ভালোবাসতেন। তাই একসময় তাঁর শারীরিক অসুস্থতা দেখা দিলে রবীন্দ্রনাথ ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। প্রশান্তকুমার পালের মতে, সম্ভবত আশ্বিনের শেষে বা কার্তিকের প্রথমে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন নীতীন্দ্রনাথের অসুস্থতা উপলক্ষে। ৯ কার্তিক ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, ২৫ অক্টোবর ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার রবীন্দ্রনাথ বিলাতে জগদীশচন্দ্রকে লেখেন :
‘আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত বলিয়া আমি কলিকাতায় আসিয়াছি, প্রায় আট রাত্রি ঘুমাইতে অবসর পাই নাই। তাই আজ মাথার ঠিক নাই, শরীর অবসন্ন। কাল হইতে তাহার বিপদ কাটিয়াছে বলিয়া আশ্বাস পাইয়াছি, এখন নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সময় আসিয়াছে। মনে করিয়াছি দুই-চারি দিন বোলপুর শান্তিনিকেতনে যাইব।’
নীতীন্দ্রনাথের অসুখের সময় মৃণালিনী দেবীকে সান্ত্বনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন:
‘তুমি করচ কি? যদি দুর্ভাবনার কাছে তুমি এমন করে আত্মসমর্পণ কর তা হলে এ সংসারে তোমার কি গতি হবে বল দেখি? বেঁচে থাকতে গেলেই মৃত্যু কতবার আমাদের দ্বারে এসে কত জায়গায় আঘাত করবে, মৃত্যুর চেয়ে নিশ্চিত ঘটনা ত নেই, শোকের বিপদের মুখে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ বন্ধু জেনে যদি নির্ভর করতে না শেখ তাহলে তোমার শোকের অন্ত নেই।’
স্বামী বিবেকানন্দ
সমাজসেবক ও ধর্মপ্রচারক।
মৃত্যু : ২০ আষাঢ় ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, ৪ জুলাই ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ, রাত ৯টার সময়, মাত্র ঊনচল্লিশ বছর বয়সে।
২২ বৈশাখ ১৩১৪ বঙ্গাব্দ ‘স্বরাজ’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের একটি লেখা প্রকাশ পায়। সেই আত্মকথামূলক লেখার এক জায়গায় বিবেকানন্দের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ কতটা আহত হয়েছিলেন তার বর্ণনা পাওয়া যায় : ‘দিন কয়েকের জন্য আমি বোলপুরের আশ্রমে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া যেমন হাবড়া ইস্টিশনে পা দিলাম অমনি কে বলিল, কাল স্বামী বিবেকানন্দ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। শুনিবা মাত্র আমার বুকের মাঝে... ঠিক যেন একখানা ছুরি বিঁধিয়া গেল।’
কয়েক বছর পর ২৮ শ্রাবণ ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, ১২ আগস্ট ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে অনুষ্ঠিত একটি ছাত্রসভায়ও রবীন্দ্রনাথ অকাল-প্রয়াত স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করে বলেছেন :
‘অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিম ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।’
মৃণালিনী দেবী
রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী।
মৃত্যু : ৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, ২৯ নভেম্বর ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার, ২৯ বছর বয়সে।
১৮ অগ্রহায়ণ ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, ৪ ডিসেম্বর ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার রবীন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্রকিশোর দেবমাণিক্যকে লিখেছেন :
‘ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন সেই শোককে তিনি নিষ্ফল করিবেন না, তিনি আমাকে এই শোকের দ্বার দিয়া মঙ্গলের পথে উত্তীর্ণ করিয়া দিবেন।’
একই দিনে প্রায় একই রকম কথা লিখেছেন মোহিতচন্দ্র সেনকে :
‘ঈশ্বর আমার শোককে নিষ্ফল করিবেন না। তিনি আমার পরম ক্ষতিকেও সার্থক করিবেন তাহা আমার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিয়াছি। তিনি আমাকে আমার শিক্ষালয়ের এক শ্রেণী হইতে আরেক শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করিলেন।’
রবীন্দ্রনাথের ‘স্মরণ’ কবিতাগুচ্ছ তাঁর পত্নীবিয়োগের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। ‘স্মরণ’-এ সাতাশটি কবিতা আছে। পাণ্ডুলিপির সহায়তায় তার মধ্যে উনিশটির রচনা-তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। বাকি যে আটটি রচনার তারিখ নেই, তার মধ্যে ছটি মুদ্রিত হয় ‘বঙ্গদর্শন’-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। কবিতাগুলো হলো : ১. ‘অতিথি’ [প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে যে খুলি দ্বার], ২. ‘শেষ কথা’ [তখন নিশীথ রাত্রি; গেলে ঘর হতে], ৩. ‘প্রার্থনা’ [আমার ঘরেতে আর নাই সে যে নাই], ৪. ‘আহ্বান’ [ঘরে যবে ছিলে মোরে ডেকেছিলে যবে], ৫. ‘পরিচয়’ [যত দিন কাছে ছিলে বলো কী উপায়ে] এবং ৬. ‘মিলন’ [মিলন সম্পূর্ণ আজি হল তোমা-সনে]। স্ত্রীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রচিত বলে কবিতাগুলোর মধ্যে স্ত্রী-বিয়োগজনিত বেদনার অভিঘাত স্পষ্ট।
‘উদবোধন’ [১১ পৌষ ১৩০৯ বঙ্গাব্দ] কবিতার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন: ‘দুলে রে দুলে রে, অশ্রু দুলে রে/আঘাত করিয়া বক্ষ-কূলে রে। / সম্মুখে অনন্ত লোক, যেতে হবে যেথা হোক/অকূল আকুল শোক দুলে রে, / ধায় কোন দূর স্বর্ণ-কূলে রে ॥’
‘অতিথি’ কবিতায় বলেন :
প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে যে খুলি দ্বার
আর কভু আসিবে না।
বাকি আছে শুধু আরেক অতিথি আসিবার,
তারি সাথে শেষ চেনা।
সে আসি প্রদীপ নিবাইয়া দিবে একদিন,
তুলি লবে মোরে রথে
নিয়ে যাবে মোরে গৃহ হতে কোন গৃহহীন
গ্রহতারকার পথে।
২৩ পৌষ ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, শান্তিনিকেতনে বসে লেখা রবীন্দ্রনাথের ‘একাকী’ কবিতার মধ্যে যেন স্ত্রীবিয়োগের শোক তীব্রতররূপে প্রকাশ পেয়েছে।
আজিকে তুমি ঘুমাও; আমি জাগিয়া রব দুয়ারে
রাখিব জ্বালি আলো।
তুমি তো ভালো বেসেছ, আজি একাকী শুধু আমারে
বাসিতে হবে ভালো।
১৮ অগ্রহায়ণ ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, ৪ ডিসেম্বর ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার অপর একটি চিঠিতে দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখেছেন :
‘ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন তাহা যদি নিরর্থক হয় তবে এমন বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে! ইহা আমি মাথা নীচু করিয়া গ্রহণ করিলাম। যিনি আপন জীবনের দ্বারা আমাকে নিয়ত সহায়তা করিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি মৃত্যুর দ্বারাও আমার জীবনের অবশিষ্টকালকে সার্থক করিবেন। তাঁহার কল্যাণী স্মৃতি আমার সমস্ত কল্যাণ কর্ম্মের নিত্যসহায় হইয়া আমাকে বলদান করিবে।’
‘বৌঠাকুরানিদের হাট’ [আজকাল, শারদ সংখ্যা ১৪১৭ বঙ্গাব্দ] শিরোনামে একটি লেখায় অমিতাভ চৌধুরী জানান যে মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীকে রবীন্দ্রনাথ নাকি একসময় মৃণালিনী দেবী সম্পর্কে বলেন, ‘সংসারের ভার একলা বইতে হয়েছে। এদের প্রত্যেকের সমস্তব্যবস্থা পড়া, বিবাহ, এমনকি তিনটি সন্তানের মৃত্যুর দুঃখও একলা বইতে হয়েছে। সবই করেছি কিন্তু জালে জড়াইনি। দূরের থেকে করেছি। বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে করেছি পুরুষের মতো।... চিরদিন আমি একটি জায়গায় উদাসীন, নিরসক্ত ছিলুম। সেইটেই আমার স্বভাব। ভিতরে ভিতরে দূরে থাকবার একটা অভ্যাস ছিল সব কিছু থেকেই। ...তবে সবচেয়ে কষ্ট হয় কী জানো। শুধু বলা, বলার জন্যেই। এমন কাউকে পেতে ইচ্ছে করে, যাকে সব বলা যাবে। সে তো আর যাকে তাকে দিয়ে হয় না।’
অপরদিকে প্রাগুক্ত রচনাটিতে পাওয়া যায়, অমলা দাশকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রী প্রসঙ্গে একবার বলেন, ‘দেখো অমলা, মানুষ মরে গেলেই যে একেবারে হারিয়ে যায়, জীবিত প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে কথা আমি বিশ্বাস করি না। তিনি (মৃণালিনী দেবী) এতদিন আমাকে ছেড়ে গেছেন, কিন্তু যখনই আমি কোনও সমস্যায় পড়ি, যেটা আমার পক্ষে মীমাংসা করা সম্ভব নয়, তখনই আমি তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করি। শুধু তা-ই নয়, তিনি যেন এসে আমার সমস্যার সমাধান করে দেন।’
(চলবে)






















 অঞ্জন আচার্য
অঞ্জন আচার্য



















